
যে যুদ্ধে মানুষকে হারিয়ে ছিল পাখিরা: ইমু যুদ্ধ
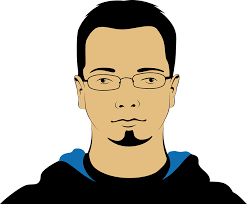
- আপডেটের তারিখ : বুধবার, ৬ এপ্রিল, ২০২২ সময় 4 years আগে
- ৩০৪ বার পড়া হয়েছে

পৃথিবীতে চলমান দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ যুদ্ধবিগ্রহ। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষে মানুষে বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ লেগেই চলেছে; এর পেছনে কখনও ছিল লোভ, কখনও ঘৃণা, কখনও কট্টর দেশপ্রেমও ছিল যুদ্ধের কারণ। তবে সব যুদ্ধই শুধু মানুষে মানুষে হয় না, প্রাণীজগতের অনেক সদস্য বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ করে। তবে আজকের আলাপ সেটা নিয়েও নয়। কখনও মানুষে-জন্তুতে যুদ্ধের কথা শুনেছেন? অস্ট্রেলিয়ার ‘ইমু যুদ্ধ’ ছিল এমনই এক যুদ্ধ। এবং এই যুদ্ধের পরিণতি আপনাকে নিঃসন্দেহে ভাবাবে ও হাসাবে।
ইমু যুদ্ধ প্রথমে আসল কোনো যুদ্ধ ছিল না। অস্ট্রেলিয়ায় ঘটেছিল এই ঘটনা, বা বলা যায় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৩২ সালে, যখন অস্ট্রেলিয়ার সরকার একটি বন্যজন্তু সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী হাতে নেয়। এর শুরুটা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ক্যাম্পিয়ন জেলায় মানুষের এলাকায় ইমু পাখিদের বিচরণ বেড়ে যাওয়ার পর।
ইমুদের কথা
ইমুদের অনেকেই উটপাখির সাথে গুলিয়ে ফেলেন অনেক সময়, এবং তাতে অল্পবিস্তর সত্যতা রয়েছে। ইমু উটপাখিদেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয়, এর বৈজ্ঞানিক নাম Dromaius novaehollandiae । এরা সাধারণত চল্লিশ কেজির কাছাকাছি ওজনের হয়ে থাকে, এবং উচ্চতায় এরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি। এরা উড়তে পারে না, তবে দৌড়াতে পারে খুব ভালো। হঠাৎ করে কাছে ছুটে আসতে দেখলে ভয় লাগারই কথা।
ইমু দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে অস্ট্রেলিয়াতেই (চিড়িয়াখানায় খাঁচার আড়ালে দেখে যদি মন না ভরে আর কী)। অস্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ পাখি ইমু। তাদের পাওয়া যায় দেশটির প্রায় সবখানেই, তবে আমাদের আজকের গল্প পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ইমুদের নিয়ে। তাদের প্রজননের মূল সময় মে ও জুন মাসে। প্রজননের পর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার শুকনো জায়গা থেকে আরও পশ্চিমে চলে যায় ইমুরা, কারণ শীতে খাবার ও পানি কমে যায়। ঐতিহাসিক মারে জনসনের মতে, এরকম এক অস্বাভাবিক পরিযানের ফলেই ইমুদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মানুষদের।
শুরুর ঘটনাবলী
সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রায় পরপরই। হাজার হাজার যুদ্ধফেরত সৈনিক, যাদের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো দক্ষতা নেই; তাদের কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে অস্ট্রেলিয়ার সরকার। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় সরকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়, ‘সৈনিক পুনর্বাসন প্রকল্প’, যার ফলে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক সৈন্য, যাদের অনেকেই ছিল ব্রিটিশ, কৃষিকাজ শুরু করে। তবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আবাদি জমির পরিমাণ অনেক কম হওয়ায় জমির বণ্টন হয়েছিল অনেকটাই অসম। এর বিকল্প হিসেবে পশ্চিমের চাষীরা উল এবং আটার চাষ শুরু করে, অনেকেই প্রচণ্ড লাভবান হন। তবে বেশিরভাগ সৈনিকেরই অবস্থা হয় শোচনীয়। জাস্টিস পাইকের মতে, ১,৪৮৫ জন সৈনিক নিজের বেশিরভাগ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ১৯২৯ সালের মধ্যেই। অনেকে আত্মহত্যাও করছিলেন। এর পরে গ্রেট ডিপ্রেশন এসে অবস্থার আরও অবনতি ঘটলো।
এরই মধ্যে আটার দাম পড়ে যাচ্ছিল আশঙ্কাজনকভাবে, যা নতুন নির্বাচিত লিওনের সরকার ঠিক করতে অক্ষম ছিল। তাই চাষীরা সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সরকার বিরোধিতার। তারা ঠিক করে তারা তাদের শস্য বেচবে না। তখন ছিল ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাস। এই টালমাটাল সময়েই পশ্চিমের প্রান্তিক এলাকাগুলোতে এক অকস্মাৎ ঝড় আসে।
সাধারণত বাঁশ ও তারকাঁটার বেড়া দিয়ে আটকে রাখা যায় ইমুদের। তবে এরকম মন্দার সময় চাষীরা বেড়ার বন্দোবস্তও করতে পারছিল না, ফলে পুরো পশ্চিমের প্রান্তিক এলাকাগুলো হয়ে উঠছিল ২০,০০০ ইমুর বিশাল বাহিনীর জন্য একটি উন্মুক্ত খেলার মাঠ।
ইমুরা অস্ট্রেলীয় আইনে প্রায় উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত রক্ষিত ছিল, ১৮৭৪ এর ‘শিকার আইন’ এর আওতায়। তবে ১৯২২ থেকেই আবাদি জমিতে তাদের উৎপাত শুরু হওয়ায় সরকার তাদের ‘ভারমিন’ বা শস্য ক্ষতিকারক প্রাণীরুপে চিহ্নিত করে, এবং এই আইনে শস্য রক্ষায় তাদের শিকার জায়েজ হয়ে যায়। এই আইন করা হয়েছিল পুনর্বাসিত সৈনিকদের অনুরোধেই। তাদের শস্য ইমুদের জ্বালায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। মারাও হয়েছিল অনেক ইমু। ১৯২৮ সালে শুধু জেরাল্ডটনের উত্তরেই প্রায় তিন থেকে চার হাজার ইমু মারা হয়েছিল। তবে ইমুদের সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে এত হত্যার পরেও তাদের সংখ্যায় কোনো বিশেষ এদিক-সেদিক হয়নি।
কিন্তু এবার সংখ্যা ২০,০০০! সৈন্যদের মাথায় হাত। ঘরে রাখা গাদা বন্দুক দিয়ে তো এদের টিকিটাও উড়ানো যাবে না, উল্টো রেগেমেগে ঘরবাড়ি তছনছ করে রেখে যেতে পারে এই বিশাল বাহিনী। এদের জন্য দরকার কামান, ভালো বন্দুক। তারা এক হয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালো পার্থ শহরে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ পিয়ার্সের কাছে। তারা তখনকার নতুন প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় বন্দুক, যাকে আমরা মেশিন গান বলে চিনি, তা দাবি করে বসলো। পিয়ার্স দেখলেন, ভারি মুশকিল! এই সৈনিকদের অনেকেই সেই যুদ্ধের সময় থেকে পরিচিত, এদের দুঃখে সমব্যথী তিনিও। তবে মন্দার এই ভয়ানক সময়ে এই অনুরোধ কি রাখা যায়? কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কথা শোনালেও তেতে উঠবে প্রশাসন।
পিয়ার্স দুই কূলই ঠিক রাখলেন। মিলিটারি বোর্ডকে না জানিয়ে বন্দুক দিলেন সৈন্যদের, একইসাথে সেখানকার পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাহায্যও মঞ্জুর করে দিলেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এর মধ্যে একেবারেই জড়ালেন না। তাদের সাথে আসলেন মেজর জি পি ডব্লিউ মেরেডিথ, সার্জেন্ট ম্যাকমারে ও গানার ও’হ্যালোরন এবং তাদের সাথে দুটো ‘লুইস মেশিন গান’ ও দশ হাজার বুলেট।
লুইস মেশিন গান
পার্থের পঞ্চম সেনা কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার মার্টিন ভেবেছিলেন, ইমুবাহিনী মারতে বেশি মেশিনগান দিলে হয়তো মাছি মারতে কামান দাগা হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি মাত্র দুটো মেশিনগান নিতে দেন। তবে তিনি হয়তো জানতেন না, ১৭৮৮ সালে মেরিন ক্যাপ্টেন ওয়াটকিন টেঞ্চ লিখেছিলেন, সিডনির ইমুরা খুবই দ্রুতগতির এবং বন্য, যার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বন্দুকের ব্যবহার খুব বেশি কার্যকর হয় না। মার্টিন হয়তো ভেবেছিলেন, এই সুযোগে তার সেনাদের ভালো শ্যুটিং প্র্যাকটিস হয়ে যাবে।
লুইস বন্দুকগুলো বানানো হতো যুক্তরাজ্যে, তবে আইডিয়াটা ছিল আমেরিকান। প্রচুর ব্যবহার হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ও ব্রিটিশপন্থী দেশের সৈনিকদের হাতে। এর মূল ডিজাইনার আইজ্যাক নিউটন লুইস। তিনি এটি আবিষ্কার করেন ১৯১১ সালে। প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০০-৬০০ রাউন্ড গুলি করা যেতো এই বন্দুক থেকে। এর ব্যবহার কোরিয়ান যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল।
যুদ্ধের প্রথম ভাগ
১৯৩২ এর ২ নভেম্বরে শুরু হয় যুদ্ধ। ক্যাম্পিয়ন থেকে সৈন্যরা ফেরত আসে। তাদের নজরে পড়ে প্রায় অর্ধ শতাধিক ইমু। তারা বন্দুকের রেঞ্জ থেকে অনেক দূরে থাকায় তাদের মারার প্রায় সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, ইমুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় চারদিকে। প্রথম দিনেই সৈন্যদের অনেক গুলি অযথা খরচ হয়, একগাদা হতাশা নিয়ে তাদের ফেরত যেতে হয়।
দ্বিতীয় দিনে সৈন্যরা গোপনে হামলার পরিকল্পনা করে একটি গুদামের পিছন থেকে। তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি। ইমুদের গতির কারণে ও মাঝপথে বন্দুক জ্যাম হয়ে যাওয়ায় প্রায় ১,০০০ ইমুর ভিড় থেকেও খুব অল্পই মারা যায়। দ্বিতীয় দিনেও প্রায় কয়েকশ রাউন্ড গুলি খরচ করে শুধু ডজনখানেক ইমু হত্যা করা যায়।
পরের কয়েকদিনও এভাবেই যায়। মেরেডিথ খেয়াল করতে শুরু করেন, ইমুদের মধ্যেও রয়েছে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও প্রকৃতিপ্রদত্ত সামরিক প্রবৃত্তি। তারা পায়ের আওয়াজ পেলেই শত শত ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক দলে একটি করে নেতা থাকে, যারা লক্ষ্য রাখে শত্রুর আগমনের, ততক্ষণে ইমুরা তাদের ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।
৮ নভেম্বরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণশীল হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, যারা এতদিন চাষীদের পক্ষেই ছিল, এই অভিযান নিয়ে আলোচনা শুরু করে। মিডিয়া এতদিনে এই অভিযান নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করা শুরু করে দিয়েছিল, যার নেপথ্যে ছিলেন সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের সাংবাদিক জর্জ ম্যাকইভার, যিনি শুরু থেকেই রক্ষণশীল সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছিলেন। তার প্রচারণায় এই ইমু যুদ্ধে বিফলতার সকল দোষ পড়ছিল সরকারের ঘাড়ে। ফলে পিয়ার্স ৮ নভেম্বর সৈন্য ও বন্দুক সরিয়ে নেন ক্যাম্পিয়ন থেকে।
যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগ

এর পরে যা হওয়ার তা-ই হলো, ইমুদের উৎপাত দ্বিগুণ হলো, চাষীরাও পুনরায় হাত পাতলেন সাহায্যের জন্য। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার (রাজ্যপ্রধান) জেমস মিচেল তার সমর্থন জানালেন তাদের পক্ষে।
এভাবে ১২ নভেম্বর সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ আবারো মঞ্জুর করলো ওই অঞ্চলে সেনা ও অস্ত্র সাহায্য। ১৩ নভেম্বর থেকে প্রথম দুদিনের অভিযান এবার বেশ ভালোই হলো, প্রায় ৪০টির মতো ইমু হত্যা করা হলো। এর পরে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০০ ইমু মারা হচ্ছিলো। ১০ ডিসেম্বর মেরেডিথ তার রিপোর্ট জমা দেন, তাতে গুলি ও হত্যার হিসেব দেয়া হয়। ৯,৮৬০ রাউন্ডে ৯৮৬টি ইমুর মৃত্যু, অর্থাৎ প্রতিটি ইমুর জন্য গড়ে ১০টি করে বুলেট খরচ হয়েছিলো।
কিন্তু এত করেও থামানো গেল না ইমুদের। প্রত্যেকবার ইমুরা যেন আরও বেশি চালাক ও কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত ফসলগুলো কোনোমতে বাঁচাতে পারলেও বছরের পর বছর ধরে ইমুদের অত্যাচার মেনেই নিতে হয় চাষীদের। সেনাবাহিনী দিয়েও প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত তাদের আটকে রাখা যায়নি। তবে এর পরে ইমুর জন্য বিশেষভাবে তৈরি বেড়ার ব্যবহার অনেক বেড়ে যাওয়ায় চাষীরা সম্ভাব্য ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জিতে গিয়েছিল ইমুরাই এই যুদ্ধে।
পরে মেরেডিথ এক পত্রিকায় বলেছিলেন,
“আমাদের যদি এই ইমুবাহিনীর একটি আলাদা দল থাকতো এবং বন্দুকধারী ইমুসওয়ার দিয়ে আমরা ওই বাহিনী সজ্জিত করতে পারতাম, তাহলে আমরা পৃথিবীর যেকোনো বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াতে পারতাম। মেশিনগানের বিপক্ষে এই বাহিনী হতো ট্যাঙ্কের মতো।”
ফিচার লেখক: আরেফিন মিজান।















